
উখিয়া নিউজ ডেস্ক::
বৃষ্টিপাত বেশি হলেই তিন পার্বত্য জেলার কোনো না কোনো এলাকায় পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে। তবে বেশির ভাগ ধসেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে না। এ কারণে ধসের বিষয়টি সবার নজরেও আসে না। ফলে আড়ালেই থেকে যায় পাহাড়িদের বসতভিটা কিংবা সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব। মৃত্তিকাবিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে সৃষ্ট ভূমিক্ষয় কিংবা পাহাড়ধসের পেছনে বসবাসকারী বাঙালি ও পাহাড়ি উভয় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী দায়ী।
পরিসংখ্যান বলছে, পাহাড় না বাড়লেও তিন পার্বত্য জেলায় ক্রমেই পাহাড়ি আদিবাসী ও বাঙালি জনসংখ্যা বাড়ছে। আর এসব জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন জুম চাষ। পাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিবছরই অপরিকল্পিতভাবে জুম চাষাবাদ হচ্ছে। কৃষক ও বাসিন্দাদের মধ্যে যুগোপযোগী চাষাবাদের জ্ঞান না থাকায় মাটির গুণাগুণও নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া বসবাসের উপযোগী স্থান গড়ে তুলতে বন উজাড় করা হচ্ছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশাল পাহাড়ে যে অনুপাতে বসবাসস্থল তৈরি করা হচ্ছে, তার চেয়েও জুম চাষ পাহাড়ধসে বেশি দায়ী। এ ছাড়া বাঁশ কোড়াল নামক সুস্বাদু রসনা বিলাসের নামে বাঁশ উজাড় করা হচ্ছে। অবাধে বন্য পশুপাখি নিধনের পাশাপাশি বসবাসস্থলের আশপাশে প্রয়োজনীয় ফল ও কাঠ গাছ রোপণ করা হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে টেকসই জুম চাষসহ বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া না হলে ফের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা মৃত্তিকাবিশেষজ্ঞদের।
এ বিষয়ে বাংলাদেশ মৃত্তিকাসম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের (এসআরডিআই) পরিচালক মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লা আমাদের সময়কে বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে নেপাল, মিয়ানমার, ভারত বা ভারতের মেঘালয় রাজ্যর পাহাড়শৃঙ্গ এখন থেকে ৫ কোটি বছর আগেকার বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে যেসব পাহাড় রয়েছে সেগুলো টারশিয়ারি যুগের। ধারণা করা হচ্ছে, এগুলোর বয়স ১ কোটি বছর। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়গুলো টিপাম সুরমা, ডুপিটিলা টিং হিং নামক গাঠনিক। এসব পাহাড়ের কোথাও কঠিন পাথর, আবার কোথাও বালুকাময় পাথর দ্বারা গঠিত। বালুকাময় পাথরের কোষে বালু থাকে বলে তা কম ক্ষমতাসম্পন্ন।
মো. দেলোয়ার হোসেন মোল্লার মতে, পাহাড় গভীর করে কেটে জুমচাষ ও বন উজাড়ের ফলে বালুকাময় পাহাড়ের মাটির উপরের আবরণ সরে যাচ্ছে। এতে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে পাহাড় ধসে পড়ছে। এ জন্য টেকসইভাবে পাহাড়ে জুম চাষবাদের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।
এসআরডিআইরের ২০১৫-১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে পাহাড়ের মৃত্তিকা উন্নয়ন অংশে বলা হয়েছে, অতীতে অধিকাংশ জুমচাষি ৬ বছরের সাইকেল চক্রে (৬ বছর পর পর) চাষাবাদ করতেন। এখন ওই সাইকেল চক্র ৩ বছরেরও নিচে নেমে এসেছে। অধিকাংশ জুমচাষি পাহাড়ের সøপে (ঢালে) চাষাবাদ করছেন। এ কারণে পাহাড়ের মাটি ক্ষয় হচ্ছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব জুম চাষের পরিবের্ত বর্তমানে পাহাড়ি এলাকায় সø্যাশ অ্যান্ড বার্ন (পাহাড়ের ছোট ছোট গাছ আগুনে পোড়ার পর চাষের জমি প্রস্তুত) পদ্ধতি বেছে নেওয়া হচ্ছে। এতে ঢালু বা উঁচু পাহাড়ের উপরের আবরণসহ মাটির গুণাগুণ নষ্ট হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে সেখান দিয়ে পানি গড়িয়ে ধসে পড়ার পেছনে অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, পাহাড়ে বাঙালি কি পাহাড়ি গোষ্ঠী, উভয়ের বাসস্থান এলাকায় সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ ফলগাছ ও কাঠগাছ রয়েছে। অথচ এসব ফল ও কাঠগাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ মাটিক্ষয় বা ধস প্রতিরোধে কাজ করে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পাহাড়ি কৃষকদের মধ্যে চাষাবাদের জ্ঞান নেই। চাষ পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিজস্ব ভাবনায় তারা ধান, ভুট্টা, তিল, মরিচ, আখ, লাউ, হলুদ, আদা, তুলাসহ অন্যান্য ফসল ফলাচ্ছে, যা পাহাড়ধসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশগত অবস্থা পরিবর্তন হলেও সেভাবে টেকসই জুম চাষ হচ্ছে না।
মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও পানি বিভাজিকা ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. মাহবুবুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, পাহাড়ের মাটি অমøীয়। মাটিতে পিএইচ মান কমলে অমøতা বাড়বে । উত্তরাঞ্চলে মাটির অমøতা গড়ে ৭.৫ থেকে ৮। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় অমøতা ৪.৫ থেকে ৫। এ কারণে পাহাড়ের মাটির গঠন দুর্বল। জুমচাষ, চাষাবাদ ও বনাঞ্চল উজাড়ের কারণে মাটির গুণাগুণ আরও দুর্বল হচ্ছে।
তিনি বলেন, আগে যেখানে ১০-১৫ বছরে একবার জুমচাষ হতো, এখন সেখানে প্রায় প্রতিবছর হচ্ছে। এতে নালা, খাদা সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে পানি জমে কর্দমাক্ত হওয়ার পর ধসে পড়ছে। তার মতে, জুম চাষ আগে পাহাড়িরা শুরু করেছে। এখন বাঙালিরাও করছে। শিল্পায়ন হচ্ছে। পর্যটন স্থাপনা হচ্ছে। বিত্তবানদের জন্য রিসোর্ট হচ্ছে। এসব কারণেই মূলত পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটছে।
মো. মাহবুবুল ইসলাম বলেন, পাহাড়ে সেটেলার হিসেবে বাঙালিরা বসবাস শুরু করলেও তাদের মধ্যে চাষাবাদের জ্ঞান থাকলেও বসবাসের প্রশিক্ষণ নেই। সে কারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে বাঙালিরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ জন্য বাঙালিদের পাহাড়ে বসবাসের উপযোগী বা বিপর্যয় প্রতিরোধী করণীয় প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন তিনি।
সংশ্লিষ্টদের মতে, পাহাড়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সক্ষমতা না থাকায় গত ৬ বছরে ধসের কারণে নিহত ১৬৬ জনের মধ্যে ১০৬ জনই বাঙালি। সম্প্রতি ভয়াবহ পাহাড়ধসে তিন জেলায় নিহত ১১১ জনের মধ্যে ৫৩ জনই বাঙালি।
পার্বত্য জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পাবর্ত্য জেলায় ১২টি ভিন্ন ভাষাভাষী পাহাড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। পাহাড়ি-বাঙালি মিলিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ লাখ। এ ছাড়া বাস্তুচ্যুত হয়ে গত এক দশকে পাহাড়ে ঢুকে পড়েছে মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যের রাখাইন, সিলেটের মণিপুরি ও খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠী। তারাও পাহাড় উজাড় করে জুমচাষ করছে।
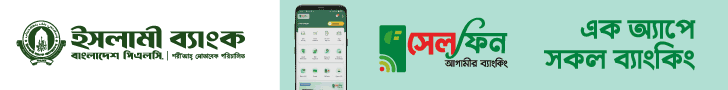


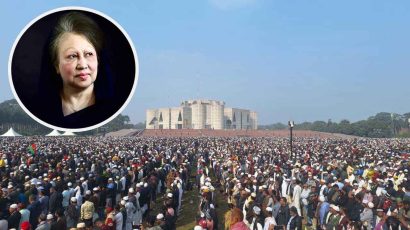






পাঠকের মতামত